সমোচ্চারিত শব্দের বানান, প্রয়োগ-রীতি ও অর্থ-ভিন্নতা
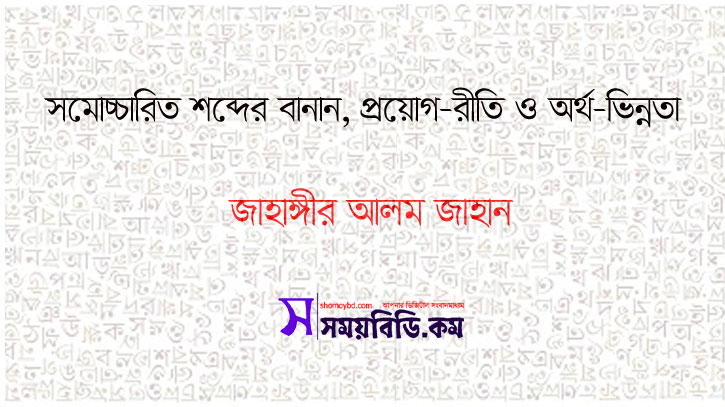
বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, যে যা-ই বলুন-না কেন, কথনের ভাষা এবং লিখনের ভাষা সবসময়ই ভিন্ন হবে। সুতরাং কথনের ক্ষেত্রে না হলেও লিখনের সময় অবশ্যই ভাষার শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। সমোচ্চারিত শব্দ লেখার সময় অনেকেই সেই শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারেন না। বিভ্রান্তিতে পড়ে প্রায়ই ভুল করে বসেন।
বাংলা ভাষায় সমোচ্চারিত শব্দের সংখ্যা অনেক। সমোচ্চারিত শব্দ বলতে সেই শব্দকে বোঝায় যে শব্দ উচ্চারণের সময় ধ্বনির দিক থেকে প্রায় অভিন্ন শোনালেও অর্থের ভিন্নতা রয়েছে। সমধ্বনির কারণে এ ধরনের শব্দ লিখতে গিয়ে অনেকেই বানান-বিভ্রাটে আক্রান্ত হন। এ-থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?
অনেক ভাষা-বিশারদ এ-প্রশ্নে অভিধান-নির্ভরতার পরামর্শ দেন। কিন্তু হাতের কাছে অভিধান না থাকলে কিভাবে এই বিভ্রাট দূর করা যাবে- সে নিয়ে তেমন কোনো যৌক্তিক পরামর্শ নেই। কেউ কেউ ভাষাচর্চায় গভীর অভিনিবেশ ও সাবধানতা অবলম্বনের ওপর গুরুত্ব দেন। এটি নিঃসন্দেহে যৌক্তিক পরামর্শ। অভিনিবেশ ও সাবধানতাবোধ যে-কোনো সমস্যা উত্তরণে কার্যকর ও সহায়ক। বানান-বিভ্রাট এড়ানোর জন্য, বিশেষ করে সমোচ্চারিত শব্দের বানান-ভিন্নতা সম্পর্কে ধারণা তৈরির জন্য গভীর অভিনিবেশ, সাবধানতা ও সচেতনতাবোধ অবশ্যই ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে। সে কারণেই অতি সাধারণ ও বহুল ব্যবহৃত কতিপয় সমোচ্চারিত শব্দের বানান-ভিন্নতা ও অর্থের পার্থক্য নিয়ে হাল্কা আলোচনা করা যেতে পারে।
‘বিশ্বস্ত’ আর ‘বিশ্বস্থ’ নিয়ে জটিলতা ও বিভ্রান্তির অন্ত নেই। বাস্তবে দু’টি শব্দই শুদ্ধ, শুধু প্রয়োগক্ষেত্রটি আলাদা। ‘বিশ্বস্ত’ মানে বিশ্বাসভাজন বা বিশ্বাসী, আর ‘বিশ্বস্থ’ মানে বিশ্বের মধ্যে। হতাশাগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত, বিকারগ্রস্ত ইত্যাদি শব্দ সঠিক। এখানে ‘গ্রস্ত’ শব্দের অর্থ আক্রান্ত বা গ্রাস করা হয়েছে এমন। কিন্তু স্থান অর্থে শব্দের শেষে ‘স্ত’ ব্যবহার করলে ভুল হবে; এক্ষেত্রে ‘স্থ’ই সঠিক ও যথাযথ। যেমন- ‘ঢাকাস্থ পরীবাগে তার দোকান আছে’।
‘দুই প্রস্ত কাগজ’ লিখলে ভুল হবে; লিখতে হবে ‘দুই প্রস্থ কাগজ’। ‘প্রস্থ’ শব্দটি অনেক সময় চওড়ার মাপকেও বুঝিয়ে থাকে। যেমন- দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ’।
‘স্বাক্ষর’ এবং ‘সাক্ষর’, ‘প্রবাহ’ এবং ‘প্রবহ’ নিয়েও সমস্যার শেষ নেই। ‘স্বাক্ষর’ হচ্ছে দস্তখত বা সহি, আবার ‘সাক্ষর’ মানে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন বা Literate। অর্থ বুঝে প্রয়োগ করতে জানলে সমস্যা থাকার কথা নয়। ‘তিনি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন’ এবং ‘দেশে সাক্ষর মানুষের হার বেড়েছে’ বাক্য দু’টি যথাযথ শব্দ প্রয়োগে শুদ্ধতা পেয়েছে। একইভাবে ‘প্রবাহ’ মানে স্রোত বা ধারা, যা অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন গতিতে বয়ে যায় এবং ‘প্রবহ’ মানে যা প্রবাহিত হচ্ছে অথবা পুরাণে বর্ণিত সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ু বিশেষ। সুতরাং ‘প্রবাহমান’ ভুল শব্দ; সঠিক শব্দ ‘প্রবহমাণ’। একইভাবে আমরা অনেকেই ‘পরিবহন’ বানান ভুল করে লিখে থাকি। প্রকৃত অর্থে পরিবহন বানানের শুদ্ধ রূপ হবে ‘পরিবহণ’।
‘সংগঠন’ এবং ‘সংঘটন’ দু’টি পৃথক শব্দ। প্রথমটির অর্থ সম্যকরূপে গঠন বা একত্রীকরণ আর দ্বিতীয়টির অর্থ ঘটনা ঘটা। বানান এবং উচ্চারণের বৈপরীত্য থাকলেও শব্দ দু’টি ব্যবহার করতে গিয়ে অনেকেই ভুল করেন। একটু মনোযোগী হলে অনাকাঙ্খিত ভুল এড়ানো কোনো কঠিন কাজ নয়।
‘স্বপক্ষ’ এবং ‘সপক্ষ’ শব্দের ব্যবহারেও ভুলের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অথচ দু’টি শব্দের বানান ও অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। ‘স্বপক্ষ’ মানে আত্মপক্ষ আর ‘সপক্ষ’ মানে অনুকূল। নিচের বাক্য দু’টি দেখলে এর বৈপরীত্য বুঝতে সহজ হবে। ‘তিনি স্বপক্ষ ত্যাগ করেছেন’ এবং ‘মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি আজ রাষ্ট্রক্ষমতায়’। এ দু’টি বাক্যে উল্লিখিত শব্দ দু’টির প্রয়োগরীতি স্পষ্ট। শব্দের অর্থ এবং বানান জানা থাকলে শব্দ প্রয়োগে অনাহুত ভুল ঘটার সম্ভাবনা কমে আসে।
‘স্বয়ম্বর’ এবং ‘স্বয়ম্ভর’ দু’টি পৃথক শব্দ। বানান এবং উচ্চারণেও ভিন্নতা রয়েছে। প্রথমটির অর্থ আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতে পতি নির্বাচন (স্বয়ংবর-সভা)। অন্যদিকে ‘স্বয়ম্ভর’ মানে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা নিজেই নিজের প্রয়োজন নির্বাহ অথবা ভরণ-পোষণ করতে পারে এমন। এ দু’টি শব্দ লিখতেও বানান বিভ্রাটে পড়ে কেউ কেউ তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। ধ্বনিগত পার্থক্য জানা থাকলে অনাহুত তালগোল থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়।
‘সার্থক’ এবং ‘সার্থকতা’ বানান লিখতে অনেকেই অনাবশ্যকভাবে স’র সাথে ব-ফলা যুক্ত করেন। এতে করে শব্দের শুদ্ধতা নষ্ট হয়। কারণ ‘স্বার্থক’ বা ‘স্বার্থকতা’ কখনোই শুদ্ধ নয়। তবে ‘স্বার্থ’ লিখতে ব-ফলার বিকল্প নেই। ‘সার্থক’ এবং ‘সার্থকতা’কে অহেতুক ব-ফলার ভারে ন্যুব্জ করা ঠিক নয়। এ বিষয়ে সচেতনতা আবশ্যক।
‘সর্গ’ আর ‘স্বর্গ’ শব্দ নিয়েও বিভ্রান্তির অন্ত নেই। সমোচ্চারিত এই শব্দদ্বয়ের অর্থ একেবারেই আলাদা। ‘সর্গ’ শব্দের বহুবিধ অর্থ রয়েছে। যেমন-সৃষ্টি, উৎপত্তি, প্রকৃতি, নিসর্গ, নিয়ম, ত্যাগ, বিসর্জন, গ্রন্থাদির অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ। আমরা সাধারণত গ্রন্থাদির অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রেই শব্দটি বেশি ব্যবহার করি। অন্যদিকে ‘স্বর্গ’ শব্দের অর্থ জানেন না এমন লোক নেই বললেই চলে। কারণ প্রতিটি মানুষই মরণোত্তর স্বর্গপ্রাপ্তির প্রত্যাশা করে। শব্দ দু’টির অর্থ ও বানান ভিন্নতা সম্পর্কে অবশ্যই সজাগ থাকা প্রয়োজন।
ইংরেজিতে Inferiority complex বলে একটি শব্দ আছে; যার বাংলা করা হয়েছে ‘হীনম্মন্যতা’। নিজের সম্পর্কে হীনতা-বোধকেই হীনম্মন্যতা বলা হয়। এ শব্দটিকে বিকৃত করে কেউ কেউ ‘হীনমন্যতা’ লিখে থাকেন। এটি অশুদ্ধ। লেখা এবং বলার সময় শুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। তাই শুদ্ধভাবে ‘হীনম্মন্যতা’ বলাই অভিধানসম্মত।
‘জ্যেষ্ঠ’ আর ‘জ্যৈষ্ঠ’ শব্দের বানান বিভ্রান্তি প্রতিনিয়ত আমাদেরকে বিব্রত করে। ‘জ্যেষ্ঠ’ মানে বয়সে বড় বা অগ্রজ। যেমন-বয়োজ্যেষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠপুত্র। অন্যদিকে ‘জ্যৈষ্ঠ’ মানে বাংলা সনের দ্বিতীয় মাস বা জ্যৈষ্ঠ মাস। এ দু’টি শব্দ নিয়ে কম-বেশি সবার মধ্যেই বিভ্রান্তি রয়েছে। একটু মনোযোগী হলে এই বিভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।
‘লক্ষণ’ মানে চিহ্ন, নিদর্শন বা আভাস। যেমন- দারিদ্র্যের লক্ষণ। ‘লক্ষ্মণ’ মানে রামচন্দ্রের বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা। লজ্জাষ্কর ভুল; বলতে হবে লজ্জাকর। অনেকে ‘লজ্জাষ্কর’ বলে লজ্জা পেয়ে থাকেন। ‘বেশি’ আর ‘বেশী’ বানান নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে। মনে রাখতে হবে ‘বেশি’ মানে অধিক বা অতিরিক্ত, আর ‘বেশী’ মানে বেশধারী; যেমন-ছদ্মবেশী।
বাংলা অভিধানে ‘কৃতি’ এবং ‘কৃতী’ বলে পৃথক দু’টি শব্দ আছে। প্রায় সমোচ্চারিত এই শব্দদ্বয়ের অর্থগত পার্থক্য থাকলেও অনেকেই লেখার সময় দু’টি শব্দকে গুলিয়ে ফেলেন। তারা হয়তো জানেন না যে, ‘কৃতি’ মানে নির্মাণ, রচনা বা সম্পাদিত কর্ম (সুকৃতি)। অন্যদিকে ‘কৃতী’ শব্দের অর্থ কর্মকুশল, কৃতকার্য বা গুণবান। হ্রস্ব ই-কার এবং দীর্ঘ ঈ-কারের গুরুত্বকে এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। তা নইলে এ শব্দ দ্বারা অর্থগত পার্থক্য বোঝানো কখনোই সম্ভব নয়। ‘কবিকৃতি’ এবং ‘কৃতী পুরুষ’ শব্দদ্বয় এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য দু’টি উদাহরণ। তবে ‘কৃতিত্ব’ লিখতে হ্রস্ব ই-কারের বিকল্প নেই। এ শব্দে দীর্ঘ ঈ-কার ব্যবহার করলে শব্দটি কৃতিত্ব হারিয়ে অর্থহীন হতে বাধ্য। কারণ অভিধানে ‘কৃতিত্ব’ থাকলেও ‘কৃতীত্ব’ শব্দের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না।
‘শিকার’ এবং ‘স্বীকার’ শব্দদ্বয়ের মধ্যে ধ্বনিগত পার্থক্য নেই বললেই চলে। কিন্তু বানান ভিন্নতা এ দু’টি শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দান করেছে। ‘শিকার’ মানে বধ করা (Hunting) অথবা দুষ্কর্মের লক্ষ্য। যেমন- ‘সে হরিণ শিকারে বেরিয়েছে’ অথবা ‘পরিস্থিতির শিকার হয়ে তার অবস্থা লেজেগোবরে হয়ে গেছে’। অন্যদিকে ‘স্বীকার’ মানে মেনে নেওয়া, সম্মতি দান বা অঙ্গীকার। যেমন- ‘অপরাধ স্বীকার’ বা ‘কৃতজ্ঞতা স্বীকার’। শব্দার্থ জানা না থাকায় অনেকে শব্দ দু’টির প্রয়োগ নিয়ে বিভ্রান্তিতে ভোগেন। একটু সচেতন হলে অনাকাঙ্খিত বিভ্রান্তি দূর করা কঠিন কাজ নয়।
‘সান্ত্বনা’ শব্দের সাথে আমরা সবাই পরিচিত। প্রতিনিয়ত কথায় এবং লেখায় আমরা এ শব্দটি ব্যবহার করি। কিন্তু শব্দটির মধ্যবর্তী বর্ণে একাধিক ‘ফলা’ যুক্ত হওয়ায় লেখার সময় প্রায় সকলেই আমরা ভুল বানান লিখে ফেলি। ন’র সাথে ‘ত’ এবং ব-ফলা যুক্ত করার কথা অনেকেরই মনে থাকে না। এমনকি কেউ কেউ এককাঠি এগিয়ে লিখে ফেলেন ‘শান্তনা’। ‘শান্তনা’ লিখলে ‘শান্ত-না’ বা ‘অশান্ত’ শব্দেরই প্রতিচিত্র ফুটে ওঠে। যা ভয়ানক অবস্থাকেই নির্দেশ করে। আমাদের শহরে একটি বাড়ির নাম রাখা হয়েছে ‘শান্তনা’। বাড়ির মালিক হয়তো ‘সান্ত্বনা’ বানানটিই ভুল করে লিখিয়েছেন ‘শান্তনা’। ফলে বাড়ির শান্তি সম্পর্কে কৌতূহল জাগতেই পারে।
‘স্মরণ’ মানে স্মৃতি। যেমন- তিনি একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। অন্যদিকে ‘শরণ’ মানে আশ্রয়। যেমন- ‘মরণ মাঝারে শরণ দাও হে’ (রবীন্দ্রনাথ)। এছাড়া ‘শরণাপন্ন’ এবং ‘শরণার্থী’ শব্দ তো আছেই। অনেকে ‘অনুসরণ’ লিখতে গিয়ে স’র সাথে ম-ফলা অথবা ব-ফলা যুক্ত করে দেন, যা ভুল। ইংরেজি শব্দের বাংলা রূপ লিখতে ‘অনুসরণ’ই শুদ্ধ। রাস্তা অর্থে ‘সরণি’ লিখতে অনেকে ভুল করে ‘স্মরণী’ বা ‘স্বরণী’ লেখেন, এটিও ভুল। প্রকৃত শব্দ হবে ‘সরণি’।
‘সত্ত্ব’ এবং ‘স্বত্ব’ সমোচ্চারিত পৃথক দু’টি শব্দ। সত্ত্ব মানে সত্তা বা অস্তিত্ব। ‘বারবার বলা সত্ত্বেও সে আমার কথা শুনল না’ অথবা ‘তৎসত্ত্বেও তিনি বেরিয়ে গেলেন’। সত্ত্ব শব্দটি আমরা সাধারণত এ ধরনের বাক্যে প্রয়োগ করে থাকি। অন্যদিকে ‘স্বত্ব’ মানে ধন-সম্পত্তিতে স্বামিত্ব বা মালিকানা। যেমন- গ্রন্থস্বত্ব বা স্বত্বাধিকারী। এ দু’টি শব্দের বানান লিখতে গিয়ে অনেকেই তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। একটু সতর্ক থাকলে ভুল ঘটার সম্ভাবনা কমে আসবে। অস্তিত্ব অর্থে ‘সত্তা’ লিখতেও কেউ কেউ ব-ফলা প্রয়োগের দিকে ঝুঁকে পড়েন। মনে রাখতে হবে ‘সত্তা’র সাথে কখনও ব-ফলা হবে না। যেমন-রাষ্ট্রিয়সত্তা, ব্যক্তিগত সত্তা ইত্যাদি।
‘সূচি’ অর্থ জ্ঞাপনী, তালিকা বা যা দ্বারা সূচনা করা হয় (Index) যেমন-সূচিপত্র বা পাঠ্যসূচি। অন্যদিকে ‘সূচী’ মানে সেলাই করা; যাকে বলা হয় ‘সূচীকর্ম’। এর বাইরে ‘শুচি’ বলে আরও একটি শব্দ আছে; যার অর্থ পবিত্র, শুদ্ধ বা নির্মল। যেমন-শুচিস্মিত বা কুটিলতাবর্জিত হাসি। এ শব্দগুলো লিখতে গিয়েও প্রায়শ ভুল করার প্রবণতা দেখা যায়। শুদ্ধতার স্বার্থে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।
‘ক্রীত’ মানে ক্রয় করা হয়েছে এবং ‘কৃত’ মানে কাজটি করা হয়েছে। শব্দ দু’টিতে বানানের পার্থক্য থাকলেও উচ্চারণের ক্ষেত্রে খুব একটা পার্থক্য নেই। সুতরাং ‘ক্রীতদাস’কে ‘কৃতদাস’ এবং ‘কৃতকর্ম’কে ‘ক্রীতকর্ম’ লেখা ঠিক নয়। একইভাবে ‘বিক্রিত’ আর ‘বিকৃত’ শব্দের অর্থগত পার্থক্যটিও মনে রাখা জরুরি। সমোচ্চারিত ধ্বনির কারণে শব্দের বানান লেখায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। একটু সচেতন থাকলে অনেক বিভ্রান্তিই পরিহার করা সম্ভব। ‘বিক্রিত কাঁচামাল’ অনেক সময় পচে গিয়ে ‘বিকৃত মাল’ হয়ে যায়। তাই বলে বানান বিভ্রাটের মাধ্যমে ‘বিক্রিত’কে ‘বিকৃত’ করা ঠিক নয়।
মিলিত হওয়া বা তীরবর্তী হওয়া বোঝাতে ‘ভিড়’ বানান ব্যবহার করাই উত্তম। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘তরণী ভিড়াও তীরে’। কাউকে দলে ভিড়ানো হলে সেক্ষেত্রেও হ্রস্ব ই-কার দিয়ে ‘ভিড়ানো’ লেখাই সঙ্গত। অপরদিকে বহুলোকের বিশৃঙ্খল সমাবেশ বোঝাতে ‘ভীড়’ শব্দই যথাযথ। ‘লক্ষ লোকের ভীড়ে সে অবলীলায় ভিড়ে গেল’। ‘ভীড়’ আর ‘ভিড়’-এর পার্থক্য বুঝতে এ বাক্যটি মনে রাখাই যথেষ্ট।
‘কুল’ আর ‘কূল’ শব্দের বানান বিভ্রাট প্রায়শই লক্ষ করা যায়। বরইফল, জাত-বংশ আর নদীর তীর বোঝাতে ‘ক’ বর্ণে কখন হ্রস্ব উ-কার এবং কখন দীর্ঘ ঊ-কার দিতে হবে- এ নিয়ে বিভ্রান্তির অন্ত নেই। বিষয়টি মনে রাখার জন্য স্মরণশক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। মনে রাখতে হবে ‘ক’ বর্ণে হ্রস্ব উ-কার দিলে যে ‘কুল’ তৈরি হয় তার অর্থ কখনও বরইফল, কখনও জাত-বংশ। যেমন-‘কুলগাছ’ অথবা ‘শ্যাম রাখি না কুল রাখি’ (জাত-বংশ অর্থে)। আবার ‘ক’ বর্ণে দীর্ঘ ঊ-কার দিয়ে যখন ‘কূল’ লেখা হয় তখন তা নদীর তট বা তীরকেই নির্দেশ করে। যেমন-‘নদীর কূল নাই কিনার নাই রে’ অথবা ‘একূল ওকূল দু’কূল হারিয়ে হলাম দেশান্তরী’। ‘কুল’ শব্দের আরও একটি অর্থ আছে। সেটি হলো তান্ত্রিক সম্প্রদায় বিশেষ। এই সম্প্রদায়ের গুরুকে বলা হয় ‘কুলাচার্য’। এটিও ‘ক’ বর্ণে হ্রস্ব উ-কার দিয়ে লিখতে হয়। একমাত্র নদীর তট বোঝাতে ‘ক’ বর্ণে দীর্ঘ ঊ-কার দিয়ে ‘কূল’ লেখা অভিধানসম্মত। এটুকু মনে রাখতে পারলে ‘কুল’ আর ‘কূল’ শব্দের বানান বিভ্রাট এড়ানো সহজ হবে।
বাংলা ভাষায় ‘সপত্নী’ এবং ‘সপত্নীক’ বলে দু’টি শব্দ আছে। এ দু’টি শব্দও অনেকের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। অনেকেই শব্দ দু’টিকে সমার্থক বলে বিবেচনা করেন। বাস্তবে শব্দ দু’টি একরকম শোনালেও দু’টির অর্থ প্রচণ্ডরকম দ্বান্দ্বিক ও পরস্পর বিরোধী। ‘সপত্নী’ শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘সতিন’। আর ‘সপত্নীক’ মানে সস্ত্রীক বা স্ব-পত্নীর সহিত। সুতরাং আমরা প্রিয়জনকে ‘সপত্নী’র চেয়ে ‘সপত্নীক’ দেখতেই বেশি পছন্দ করব। তাই শব্দ দু’টির অর্থ অবশ্যই জানা থাকা জরুরি।
অনেকে ‘স্বপরিবার’ এবং ‘সপরিবার’ নিয়েও দ্বন্দ্বে ভোগেন। ‘তিনি স্বপরিবারে বেড়াতে গিয়েছেন’ বললে বুঝতে হবে যে, তিনি নিজের পরিবার নিয়ে বেড়াতে গিয়েছেন। ‘তিনি সপরিবারে বেড়াতে গিয়েছেন’ বললে পরিবারসহ বেড়াতে গিয়েছেন বলেই বুঝতে হবে। সোজা কথায় ‘স্বপরিবার’ মানে নিজ পরিবার, আর ‘সপরিবার’ মানে পরিবারসহ। শব্দ দু’টির বানান ও প্রায়োগিক ক্ষেত্র সম্পর্কে সচেতন থাকলে আমরা অনেক ভুলকে এড়িয়ে যেতে পারি। একইভাবে ‘স্ববান্ধব’ আর ‘সবান্ধব’ শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কেও আমাদেরকে সচেতন হতে হবে।
‘নিচ’ এবং ‘নীচ’ নিয়েও অনেক সমস্যা ঘটে। অভিধান মতে দু’টি বানানই শুদ্ধ; তবে প্রয়োগক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা আছে। ‘নিচ’ মানে নিচা বা নিম্নস্থান। অন্যদিকে ‘নীচ’ মানে হীন, নিকৃষ্ট, ইতর। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ‘নিচুস্থান’ বোঝাতে ‘নিচ’ লেখাই অধিকতর সঠিক। যেমন-‘তিনি উপর থেকে নিচে নেমে এলেন’। এরূপ ক্ষেত্রে হ্রস্ব ই-কার দিয়ে ‘নিচ’ লেখাই শ্রেয়। আবার ‘তুমি এত নীচ’ কিংবা ‘নীচকুলে জন্ম নিয়েও সে অনেক মহান’ এরূপ ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঈ-কার ব্যবহার করাই যথার্থ। নীচতা শুদ্ধ, কিন্তু নিচতা অশুদ্ধ।
‘বদলি’ এবং ‘বদলী’ শব্দের ধ্বনিগত উচ্চারণ প্রায় অভিন্ন। ফলে এ দু’টি শব্দের প্রয়োগ-রীতি নিয়ে অনেকেই সমস্যায় ভোগেন। অনেকে এটিকে একই অর্থবোধক বলেও ভুল করেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দ দু’টির বানান ভিন্নতা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে অর্থেরও ভিন্নতা। ‘বদলি’ শব্দটি ইংরেজি Transfer শব্দের বঙ্গানুবাদ। অন্যদিকে ‘বদলী’ মানে একজনের স্থলে অন্যের শ্রম বিনিয়োগ; অনেকটা ইংরেজি ‘On behalf of’-এর মতো। সোজা কথায় যাকে বলা হয় বদল খাটা বা বদলী খাটা। যেমন-বদলী কামলা বা বদলী শ্রমিক। উদাহরণ হিসেবে দু’টি বাক্যের উদ্ধৃতি দেয়া হলো; ‘তাকে রাঙ্গামাটি বদলি (Transfer) করা হয়েছে’ এবং ‘সে তার বাবার হয়ে বদলী কাজ করছে’ (He is working on behalf of his father)।
‘দাঁড়ি’ এবং ‘দাড়ি’ নিয়েও বিভ্রান্তির অন্ত নেই। চন্দ্রবিন্দুহীন ‘দাড়ি’ মানে ‘শ্মশ্রু’; যেমন- দাড়িওয়ালা লোক। ‘দাড়ি’ শব্দে যখন চন্দ্রবিন্দু ভর করে তখন সেটি যতিচিহ্ন বা পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন ‘দাঁড়ি’ (।) হয়ে যায় । ‘দাঁড়ি’ শব্দটি অনেকসময় তুলাদণ্ড বা ‘দাঁড়িপাল্লা’র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। আবার দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে ‘দাঁড়ী’ লেখা হলে সেটি নৌকার দাঁড়টানা ব্যক্তিকে বোঝায়। বানানের এই বৈপরীত্য ও প্রায়োগিক ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রত্যেকেরই সচেতন থাকা উচিত।
‘দার’ মানে স্ত্রী বা পত্নী। যেমন- দার পরিগ্রহ বা বিবাহ। যিনি ‘দার’ অথবা পত্নী গ্রহণ করেন না তাকে বলা হয় ‘অকৃতদার’। আবার ‘দ্বার’ মানে দরজা। যেমন- প্রবেশদ্বার। এই বানান-ভিন্নতা সম্পর্কে সকলেরই অবগত থাকা দরকার।
পল্লীকবি জসীম উদ্দীন-এর ‘কবর’ কবিতায় ‘দেড়ি’ বলে একটি অপ্রচলিত শব্দ রয়েছে। শব্দটি অনেককেই ভাবিত করে। কারণ এই শব্দটি অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায় না। ‘শাপলার হাটে তরমুজ বেচি দু’পয়সা করি দেড়ি/পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হতো না দেরী’। লক্ষণীয় যে, ‘দেড়ি’ শব্দের সাথে ‘দেরী’ শব্দের অন্ত্যমিল দেওয়া হয়েছে। ‘দেরী’ না-হয় বোঝা গেল ‘বিলম্ব’ (যদিও আজকাল ‘দেরি’ও লেখা হচ্ছে) । কিন্তু ‘দেড়ি’ মানে কী? কাব্য-সমালোচকেরা অবশ্য এই অপ্রচলিত শব্দেরও নিগূঢ় মাহাত্ম্য খুঁজে বের করেছেন। তাঁদের মতে, ‘দেড়ি’ অর্থ লাভ বা মুনাফা। সুতরাং ‘দেড়ি’ এবং ‘দেরী’ (অথবা ‘দেরি’) শব্দের বানান সম্পর্কেও আমাদের সচেতন হতে হবে।
‘নীর’ মানে জল বা পানি, আর ‘নীড়’ মানে পাখির বাসা। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ‘নীড়’ শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়; ‘পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন’।
পতন অর্থে ‘ঝরা’ শব্দে ‘র’ই সঠিক। অনেকে ‘ঝড়া’ লেখেন। এটি ঠিক নয়। আবার তুফান অর্থে ‘ঝড়’ সঠিক, ‘ঝর’ ভুল। ‘সমস্ত’ বোঝাতে ‘সারা’ লেখাই সঙ্গত। যেমন-‘সারাবাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা’ (জসীম উদ্দীন)। এ ক্ষেত্রে ‘সাড়া’ লিখলে ভুল হবে। ‘সারা’ শব্দের আরও কিছু অর্থ রয়েছে। যেমন- ক্লান্ত হওয়া (ডেকে ডেকে সারা), সম্পাদন করা (সময়মতো কাজ সারা), সর্বনাশ হওয়া (জুয়ায় টাকা হেরে তার কর্ম সারা), মেরামত করা (ভাঙা জিনিস সারা), সাঙ্গ বা সমাপ্ত হওয়া (‘বাদলের গান হয়নি সারা’, রবীন্দ্রনাথ) ইত্যাদি। অন্যদিকে ‘সাড়া’ শব্দের অর্থ প্রতিউত্তর; ‘ডেকে ডেকে সারা হলাম, তবু কেউ সাড়া দিল না’। শুদ্ধ ভাষাচর্চার স্বার্থে বানান ও অর্থের ভিন্নতা সম্পর্কে সকলকেই সজাগ থাকতে হবে।
বাংলা ভাষায় প্রায়শ ব্যবহৃত দু’টি সমোচ্চারিত শব্দ হচ্ছে ‘লক্ষ’ এবং ‘লক্ষ্য’। প্রথমটির অর্থ লাখ বা দেখা। যেমন- এক লক্ষ টাকা অথবা লক্ষ করা (দেখা অর্থে)। অন্যদিকে ‘লক্ষ্য’ মানে উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়। দেখা বা লাখ টাকা অর্থে ‘লক্ষ’ লিখলে তাতে য-ফলা (্য) পরিত্যাজ্য। কিন্তু উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় অর্থে ‘লক্ষ্য’ শব্দে অবশ্যই য-ফলা (্য) প্রয়োগ করতে হবে। শব্দ প্রয়োগের সময় বিষয়টি মাথায় রাখলে ‘লক্ষ’ আর ‘লক্ষ্য’ নিয়ে অনাহুত বিভ্রাট এড়ানো সম্ভব।
সজ্জা এবং শয্যা বাংলা ভাষার আরও দু’টি অতি পরিচিত শব্দ। উচ্চারণগত পার্থক্য থাকলেও অনেকেই লেখার সময় তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। ‘সজ্জা’ মানে সাজ আর ‘শয্যা’ মানে বিছানা। অর্থ জানা থাকলেও প্রয়োগের সময় অনেকেই ভুল করে বসেন। সুতরাং লেখার সময় অবশ্যই সতর্কতা জরুরি।
তড়িৎ আর ত্বরিত নিয়ে বিভ্রান্তির অন্ত নেই। ‘তড়িৎ’ মানে বিদ্যুৎ আর ‘ত্বরিত’ মানে দ্রুত বা তাড়াতাড়ি। লেখার সময় বানান সচেতনতার অভাবে প্রায়শই শব্দ দু’টির ভুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য গভীর অভিনিবেশ ও সতর্কতার বিকল্প নেই।
বাঙালিকে বলা হয় সঙ্কর জাতি। অথচ ‘সঙ্কর’ বানানটি লিখতে গিয়ে অনেকেই লিখে ফেলেন ‘শঙ্কর’। এ-যে কত বড় ভুল তা অনেকেই বুঝতে চান না। বিভিন্ন জাতের মিশ্রণে যে জাতির উদ্ভব তাকে বলা হয় ‘সঙ্কর’। অন্যদিকে ‘শঙ্কর’ মানে সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মঙ্গলকারী দেবতা বা শিব। ‘সঙ্কর’ আর ‘শঙ্কর’ নিয়ে বিদ্যমান বিভ্রান্তি দূর হওয়া খুবই জরুরি।
মরা মানে মৃত্যুবরণ করা। কিন্তু মৃতদেহ বা লাশ বোঝাতে ‘মরা’ লিখলে ভুল হবে। এক্ষেত্রে লিখতে হবে ‘মড়া’। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আছে ‘মড়ার আবার জাত কি রে’। ‘মরা’ আর ‘মড়া’ শব্দের পার্থক্যটি মাথায় রাখলে অনাহুত ভুল ঘটার সম্ভাবনা অবশ্যই কমে আসবে।
বাংলা ভাষায় ‘ধস্’ বলে একটি শব্দ আছে; যার অর্থ উপর থেকে সবেগে কোনোকিছু খসে পড়া। যেমন- পাহাড় ধস্ বা পুঁজিবাজারের ধস্। কিন্তু অনেকেই ‘ধস্’ লিখতে ‘ধ’র সাথে অনাবশ্যকভাবে ব-ফলা যুক্ত করে লেখেন ‘ধ্বস’, যা একেবারেই অশুদ্ধ। কারণ অভিধানে ‘ধস্’ থাকলেও ‘ধ্বস’ বলে কোনো শব্দ নেই। তবে ‘ধ্বংস’ লিখতে ‘ধ’র সাথে ব-ফলার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক।
অস্ত্রোপচার শব্দ লিখতে গিয়ে অনেকেই লিখে ফেলেন অস্ত্রপাচার। ‘অস্ত্রোপচার ’ যদি ‘অস্ত্রপাচার’ হয়ে যায় তাহলে অর্থের কতবড় বিভ্রাট তৈরি হয় তা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ চিকিৎসার্থ রোগীর দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ করাকে বলা হয় অস্ত্রোপচার। ইংরেজিতে যাকে Surgery বা Surgical Operation বলা হয়। অন্যদিকে চুপি চুপি অস্ত্র অপসারণ বা অস্ত্র সরিয়ে ফেলাকে বলা হয় অস্ত্র পাচার। যার ইংরেজি হতে পারে Illegal traffiking of arm. ডাক্তারের কাজ হচ্ছে রোগীকে সুস্থ করার জন্য রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করা; আর সমাজের কথিত ডন বা গডফাদারেরা করেন অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা। তাদের কাজ হচ্ছে অস্ত্র পাচার করা। সুতরাং অস্ত্রোপচার (Surgical Operation) বোঝাতে আমরা যেন কখনো ‘অস্ত্রপাচার’ না লিখি সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। নইলে শব্দটি দ্বারা আমরা কখনোই সঠিক অর্থ প্রকাশ করতে পারবো না।
‘সত্তর’ মানে ৭০ সংখ্যা; আবার ‘সত্বর’ মানে তাড়াতাড়ি বা শীঘ্র। দু’টি শব্দেই উচ্চারণগত সমিল লক্ষণীয়। অথচ বানান-ভিন্নতার কারণে দু’টির অর্থ দু’রকম। একইভাবে ‘অর্ঘ’ মানে মূল্য এবং ‘অর্ঘ্য’ মানে পূজা-সামগ্রী, যতি মানে বিরামচিহ্ন আবার জ্যোতি মানে তেজ বা দীপ্তি, বাড়ি মানে গৃহ এবং বারি মানে জল বা পানি, বেয়াড়া মানে বেঢপ বা বদ, অন্যদিকে বেয়ারা মানে পিয়ন বা বাহক, গোঁড়া মানে অন্ধবিশ্বাস এবং গোড়া মানে মূল বা শেকড়, দেশ মানে রাষ্ট্র, আবার দ্বেষ মানে ঈর্ষা বা শত্রুতা, অশ্ব মানে ঘোড়া এবং অশ্ম মানে পাথর, অসার মানে সারহীন এবং অসাড় মানে অনুভূতিহীন, ধনি মানে সুন্দরী যুবতী, ধ্বনি মানে শব্দ বা সুর, আবার ধনী মানে ধনবান ব্যক্তি, পিঠ মানে পৃষ্ঠ এবং পীঠ মানে বেদী বা প্রতিষ্ঠান, দীপ মানে প্রদীপ, দ্বিপ মানে হস্তি বা হাতি, আবার দ্বীপ মানে জলবেষ্টিত স্থান, কুজন মানে মন্দ লোক এবং কূজন মানে পাখির কাকলি, সম্মিলন মানে সম্যক্ মিলন বা বহু লোকের একত্র হওয়া, আবার সম্মীলন মানে চক্ষু বোজা।
এ-রকম সমোচ্চারিত শব্দের সংখ্যা বাংলাভাষায় এত বেশি যে, সবগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করলেও রচনার পরিধি দীর্ঘতর হয়ে যাবে। তাই বানান-সচেতন মানুষদের শুদ্ধ ভাষাচর্চা ও বানান-সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংক্ষিপ্তভাবে বক্ষমান রচনাটি উপস্থাপন করা হলো।
জাহাঙ্গীর আলম জাহান
মোবাইল: ০১৭১১-২২৩৪৬৮



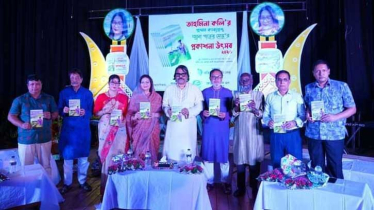
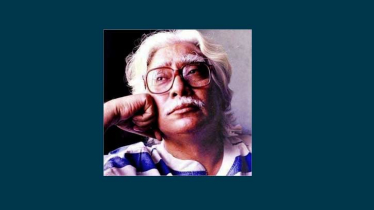
মন্তব্য করুন: